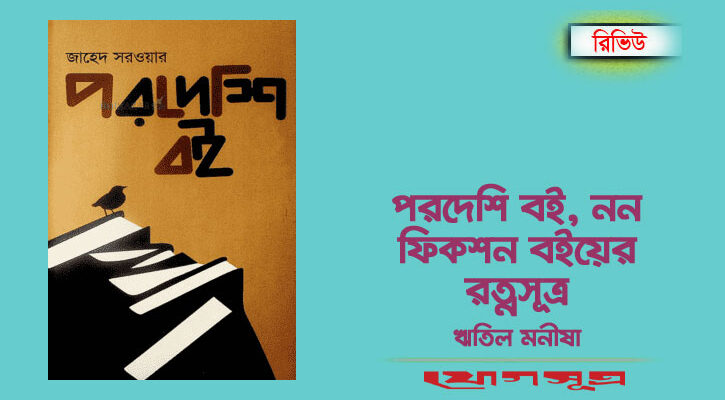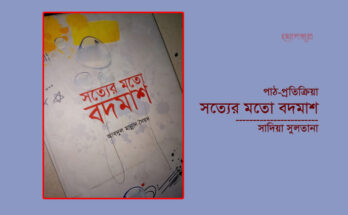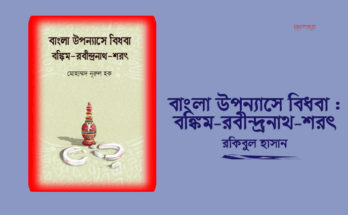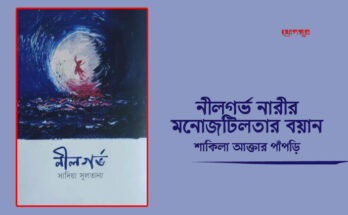কবি ও সমালোচক জাহেদ সরওয়ারের ‘পরদেশি বই’ গ্রন্থে ২৮টি বই নিয়ে আলোচনা সমালোচনা স্থান পেয়েছে। যার অধিকাংশই নন ফিকশন এবং যে বইগুলো কোন না কোন সময়ে আমরা পড়তে চাই বারবার। সান জু, কনফুসিয়াস, তাওতেচিং,প্লেটো, ভলতেয়ার, রুশো, ম্যাকিয়াভেলি, সিমোন দ্য বেভোয়া, টমাস মুর, দস্তইয়েভস্কি, তলস্তয়, বার্ট্রান্ড রাসেল, ইলিয়া এরেনবুর্গ, রাসুল গামজাতভ,গুস্তাভ লা বু, জেমস জয়েস,কাফকা,কামু,তায়েব সালেহ,হেমিংওয়ে,আর কে নারায়ণ, তেহমিনা দুররানি, নুট হামসুন, হালের অরুন্ধতি রায় পর্যন্ত। মহাকালের ধারায় জীবন কয়েকটি মুহূর্তের সমাবেশ মাত্র। মুহূর্ত থেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মুহূর্ত একেঁ এক একটি বই আবহমান চিন্তা ও সভ্যতার গতিপথ রূপে বিরাজমান।
দেশ-বিদেশের নানা বই দেশ-জাতি-গোষ্ঠী সীমা অতিক্রম করে বিশ্ব সাহিত্য অঙ্গনে একতা গড়ে তুলে। যেকোনো জাতির বই যেকোনো রাষ্ট্রীয় সীমা বাঁধা নিষেধ উপেক্ষা করে যেকোনো জাতির নবচিন্তার উন্মেষ ঘটাতে পারে। এমনকি যেকোনো ভিন্ন সময়েও যে কেউ, যে কোনো বইয়ের গহীনে প্রবেশ করে অমৃত রস আহরণ করে আত্ম উন্নয়ন ঘটাতে পারে।
যুগে যুগে মানবচিন্তার অনুঘটক বই। বই কেবলমাত্র একটি সময়ের চিত্রই নয় বরং সময়ের নিরব সাক্ষী হয়ে কালে কালে নব নব অর্থ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজ ব্যাখ্যার অগ্রসর পথ নির্দেশক।
শিল্প, রাজনীতি, ইতিহাস, ধর্ম, গল্প ইত্যাদি সাহিত্যের নানাবিধ প্রকরণকে এক পাতে রচে কবি, সমালোচক ও প্রাবন্ধিক জাহেদ সরওয়ার সাহিত্য সাধনারত কৌতূহলী ও অনুসন্ধিৎসু মানুষের মনের অলিতে-গলিতে দৃষ্টিপাত করে বাড়িয়ে দিয়েছেন পাঠকের মনের ক্ষুধা৷ এই ক্ষুধায় স্বাস্থ্যহানীর ভয় নেই বরং সমৃদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ষোলআনা।
ভৌগলিক ও সময়ের পরিসীমাকে ভেঙে চূড়ে বই সাধকের সাহিত্য সাধনার গতিপথকে সুদূরপ্রসারী করার উদ্যোগ হিসেবে প্রাবন্ধিক ঢুকে পড়েছেন শিল্প সাহিত্য কলার সদর দরজা চৌকাঠ পেরিয়ে অন্দরমহলে।
এক শেকড়ে লিপিবদ্ধ বইয়ের এ যাত্রায় কবি, প্রাবন্ধিক জাহেদ সরওয়ারের সফর সঙ্গী হয়ে আমরা শুরুতেই মুখোমুখি হই ‘নান্দনিক যুদ্ধ বিদ্যা’র সুনিপুণ কৌশলী সমরদক্ষ চিন্তক চান জু’ র (Sun Tzu)। পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধ বিদ্যার রণ কৌশল প্রণালী’র এই বইটির কদর উত্তর পশ্চিম মিলিটারি শিক্ষা ব্যবস্থার ও লাইফস্টাইলের এক অনবদ্য আলোড়ন। অতীতেও যেমন রাষ্ট্রের সীমা রক্ষী বাহিনীর ট্রেইনিংএ সমাদৃত ছিল আজও এ বইটি শুধুমাত্র তৎসংশ্লিষ্ট মানুষের কাছে নয়, সব ধরনের পাঠকের কাছেও সম কৌতূহল উদ্দীপক।
রণকৌশলপর সমরনীতির দার্শনিক অভিমুখে ষোড়শ শতাব্দীতে এসে দেখা মিলে ম্যাকিয়াভেলীর ‘প্রিন্স’ এ। ধর্ম রাজনীতি প্রপাগাণ্ডা ব্যবহার করে শাসককে মূর্ত অভিনেতা ও ঘোরতর ক্ষমতা ব্যবহারকারীর ভূমিকা পালন করতে হবে। আধুনিক রাজনীতির দার্শনিক স্কুলে সম্মান ও শক্তির ব্যবহার, প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণের কার্যপ্রণালী নির্ধারক বইটির অবদান সন্দেহাতীত। অপরিসীম দক্ষতায় ম্যাকিয়াভেলির রাষ্টীয় নীতিমালার স্বভাব চরিত্র গঠন সম্পর্কিত উপদেশের প্রভাব পশ্চিম দেশের রাজনৈতিকদের কাছে আজও ‘প্রেসক্রিপশন’ এর মতো৷
রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে দর্শনের প্রথম দিকের আলোর দিশারী প্লেটোর কথা ছাড়া দর্শনের ধারাবাহিক ইতিহাস জ্ঞান সম্ভব নয়। প্লেটোর ব্যাপক গবেষণার বিষয় বলয় থেকে জাহেদ সরওয়ার বেছে নিয়েছেন বহুল আলোচিত একাধারে মডার্ণ ও ক্ল্যাসিক প্রেম সম্পর্কিত তর্ক যুদ্ধ প্লেটো বা প্লাতনের সিম্পোজিয়াম ‘প্রেম রসিক হব কেমনে?’ শিরোনামে।
আলোচনায় উঠে এসেছে যৌনতা-লিঙ্গ-সহজাত প্রবৃত্তি বোধ, অনুভব উপযোগিতা। পরিবেশনে প্লেটো যত না দার্শনিক তারচেয়ে সাহিত্য গুনে গুনিন। চরিত্র গঠনে প্রয়োগে, কথোপকথনে পানাহারে ভোজনে বৈঠকী ঠমকে দৃশ্য পরম্পরা এ যুগেরও সিনেমাটিক চিত্রায়ন যেন। এসেছে সাধারণ গৃহজীবী প্রেম থেকে শুরু করে উচ্চমার্গীয় দেহ উপেক্ষাকারী মানসিক প্রেম ও সম লিঙ্গ প্রেমের ব্যক্তিক ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তা এবং বিরোধিতা। তবে চরিত্রগুলো সব পুরুষই, প্রেমের ব্যাপারে নারীর মন ও মন্তব্যের প্রকাশ এখানে নেই।
গত শতাব্দীর ৯০ এর দশকে প্রেমের বৈচিত্র্যের আরেকটি প্রকাশ দেখি প্রেমের আগ্রাসী পুরুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ গল্পের বয়ানে আত্মজীবনীমূলক লেখা ‘মাই ফিউডাল লর্ড’ এ তেহমিনা দূররানীর পাকিস্তানে। দেখি আরেকটি সাম্রাজ্যবাদের পচনশীল ভূয়ো আদর্শের শিকার দেশের রাজনীতি মঞ্চে কুশলী নেতাদের ভণ্ডামির ও ছলচাতুরীর খেলায় শ্বাসরুদ্ধকর নারীর অবস্থান। পাশাপাশি এলিট শ্রেণির নারীদের শিক্ষা দীক্ষায় পারদর্শী হয়ে উঠেও ধন-সম্পদের কাছে নিরাপত্তার চাবিকাঠি আছে ধরে নিয়ে তথাকথিত স্বাধীনতা চর্চার ভণিতা ও ভণ্ডামির অন্তঃপুর তেহমিনা এই বইটিতে অবলীলায় সাধারণ মানুষের চোখে উদঘাটন করেছেন।
জাহেদ সরওয়ারের ভাষায়, সাম্প্রতিক সময়ের সর্বাধিক পঠিত বইগুলোর মধ্যে এটি জায়গা করে নেয় তার গল্পবলার বিশ্বাস যোগ্যতার কারণে৷ আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র বোধে দাম্ভিক সমাজে কেবল নারীই নয়, ফেঁসে গেছে গোটা মানব সমাজ৷ চেতনা ও সামাজিক দ্বন্দ্ব এবং তৎসংলগ্ন ব্যক্তিক আকাঙ্খা মানুষকে আত্মিক যে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নিয়ে যায় কাফকার ‘অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের সংকট’ যেন সে ধারারই মূর্তমান উদাহারণ।
পরিচিত পৃথিবীর বদলে যাওয়া পরিবেশ, সামাজিকতা ও পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত যেন আমাদের সেই যক্ষের বুড়ির মত প্রাচীন প্রবাদকেই বিবর্তন করে গড়ে উঠে যার কেন্দ্রে কালস্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া নিজেকে অনেকটা ভাগ্যের হাতের পুতুলের মতই ‘কিছু করার নেই’ অবস্থায় নিয়ে যায়। সংগ্রামশীলতা মানব চেতনার অংশ তার বিপরীতে সমাজ ও পরিবারের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে আরোপিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমরা ডুবে যাই নির্বিকার অন্তহীন অর্থহীনতায়৷ তারপরও কাফকার নব সাহিত্যের ধারার কৃতিত্ব হচ্ছে বিষাদের রসে পূর্ণ গ্লাসে একাত্ম হয়ে আমরা তার বেদনার শামিল না হয়ে পারি না। যেমনটি পারি না উপেক্ষা করতে সাত্রের ফিলজফির জলন্ত নায়ক সৃষ্টিকারী কাম্যুর ‘দ্য আউটসাইডার’ বা আগন্তুকের নিরবচ্ছিন্ন অনুভব বা সহানুভূতির অসংযোগ সাধনা।
যে কারণে সমস্ত সুবোধ শব্দগুলো আমাদের কচ্ছপের মতো খোলসে ঢুকিয়ে নিজেদের কামনা ও লোভ লুকিয়ে আরও ছলচাতুরীতে পারদর্শী হতে সাহায্য করে। কাম্যুর নায়ক তাই পোশাকি ভাষার ব্যবহারে ছুরি চালিয়ে আধুনিক ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্যতার সৎ ও নগ্নপ্রকাশ।
সবকিছুর পরেও শূন্যতা আমাদের মুক্তি হতে পারে না, এইদিকে দৃষ্টিপাত করে প্রাবন্ধিক রুশোর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ‘মানুষ জন্মায় স্বাধীন কিন্তু সর্বত্র শৃঙ্খলিত।’
রুশো মানুষকে তার জন্মের পূর্বেই শ্রেণিকরণ থেকে মানুষের চিন্তা চেতনাকে নিয়ে এসেছে সাধারণ ও স্বাভাবিক কার্যকারণ সূত্রে। কোন সার্বভৌমত্ব রুশো মানুষকে তার জন্মের পূর্বেই শ্রেণিকরণ থেকে মানুষের চিন্তা চেতনাকে নিয়ে এসেছে সাধারণ ও স্বাভাবিক কার্যকারণ সূত্রে। কোনো সার্বভৌম রাজনীতি গোষ্ঠী সাধারণ মানুষের ভাগ্য বিধাতা হয়ে দাঁড়াতে পারে কি না, এই প্রশ্নটিকে যথাসম্ভব চুলচেরা বিশ্লেষণ করে রুশো এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে রাষ্ট্র জনগণকে দাস বানিয়ে যা ইচ্ছে করতে পারে না বরং ‘সার্বভৌম জনগণ ইচ্ছে করলে যেকোনো সময়ই সরকারকে সীমাবদ্ধ, সংকুচিত, শোধন ও পুনরুদ্ধার করতে পারে’। জনগণের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা চর্চা ‘সাধারণ ইচ্ছা’ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে প্রত্যেকেই স্বাধীন বিশ্বাসে সম অবস্থান করতে পারে৷ আজও সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে সুশৃঙ্খল সমাজ গঠন চিন্তায় রুশোর ‘সোশ্যাল কন্টাক্ট’ একটি আশ্চর্য দস্তখত হয়ে রয়েছে।
রুশোর মতো ‘এনলাইটেন মানুষ’ মানবসমাজ উন্নয়নে উন্নততর human quality’র জন্য লড়াই করে গেছেন তারপরও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসেও তার চিন্তা নারীর বেলায় দ্বিচারিতার শামিল। রুশোর মানব, পুরুষ আর মানবী শারিরীক আর মানসিকভাবে দূর্বল নারী।
‘নারীকে টিকে থাকার জন্য পুরুষের ওপর নির্ভর করতে হবে কেন?’ হঠাৎ গলা ফাটিয়ে সবার কর্ণগোচরে তাই দ্য সেকেন্ড সেক্সের সিমোন দ্য বেভোয়ার উচ্চকিত স্বরে সত্য প্রকাশ করতে গিয়ে বলে, কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, নারী হয়ে উঠে। শিশুকে না দেখিয়ে দিলে শিশু বুঝতে পারে না, সে নারী নাকি পুরুষ! বড় হতে হতে মানব শিশু শিখতে থাকে, নারী ও পুরুষের সামাজিক অবস্থানের মত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে অনেক কিছুই আলাদা। এই ব্যক্তিমালিকানার সমাজে নারীও যেন ব্যক্তি সম্পত্তির মতোই চেতনাহীন বস্তু কোন। সিমোন বলেন, নারীর পক্ষে যা দূর্ভাগ্য বয়ে এনেছিল তা হচ্ছে শ্রমিকের সহকর্মী হতে না পারার জন্য সে বাদ পড়ে যায় মানবিক সহচারিতা থেকেও। নারীর মুক্তি ঘটতে পারে তখনই যখন নারী বৃহৎ সামাজিক মাত্রায় উৎপাদনে অংশ নিতে পারবে। গৃহস্থালির কাজে অংশ নেবে নগন্য মাত্রায়।
প্রসঙ্গত, সমসাময়িক নারীবাদ নিয়ে যারা ভাবে, তাদের মনে রাখা উচিত পুরুষেরা যা যা করে স্বাধীনতা চর্চা করে সমাজে সবকিছুই গোটা মানব সমাজের জন্য ইতিবাচক নয়, আর মানব সভ্যতার জন্য নেতিবাচক এমন কিছু করা নারী স্বাধীনতার চর্চার অংশ হতে পারে না। আবার পুরুষকে পদদলিত করার মধ্য দিয়ে নারীর মুক্তি অর্জন নয়, বরং নারী ও পুরুষের সম অর্থনৈতিক কাজের সুযোগই তাদেরকে মানসিকভাবে আরও কাছকাছি পরস্পরকে বুঝতে ও বোঝার ব্যবধান ঘুচাতে সাহায্য করবে।
চেনা ছকের বাইরে গিয়ে সমস্ত অক্ষম, অর্ধসমাপ্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গুর পঙ্গু বৈষম্যের সমাজে দাড়িয়ে পূর্ণ, সমাপ্ত, সুখী এক সমাজের কথা আমরা না ভেবে পারি না। সেই সম্ভাবনা ও সমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সুন্দর কাল্পনিক টমাস মুরের ইউটোপিয়া সমাজ। ইউটোপিয়া কোন বৈজ্ঞানিক সমাজের নিয়মভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হলেও মুরের ১৫১৬ সালে প্রকাশিত ইউটোপিয়া বইটির প্রভাব পরবর্তীকালে সাঁ-সিমোঁ, ফুরিয়ে, ওয়েনের শান্তিপূর্ণ এবং ভেইটলিং এর হিংসাত্মক পন্থায় বিপ্লবের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্র চিন্তায় প্রভূত প্রভাব ফেলে।
প্রাবন্ধিক জাহেদ সরওয়ার স্বল্প পরিসরের ‘ইউটোপিয়া বা নাইদেশের সাকিন কোথায়’ অনুচ্ছেদে টমাস মুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন স্বাচ্ছন্দ্যে তার কর্মজীবন ও জীবীকার মাধ্যমে যে জীবিকা নির্বাহ করতে গিয়ে মুর ক্ষমতাসীন মানুষের চৌর্যবৃত্তি কাছ থেকে দেখার সুযোগে অতিষ্ঠ হয়ে জনগণকে নিয়ে সুখ সন্ধান ও সমতার কথা চিন্তা করে যত্ন সহকারে গড়ে তুলেন সুপরিকল্পিত ইউটোপিয়া নগর ধারণা। যৌথ সমবায় জীবনে যা যা প্রয়োজন তা-ই যেন ‘নাইদেশ’ এর মনের কথা। কাল্পনিক হলেও ইউটোপিয়া যেকোনো মেধাবী ও সমাজ সচেতন মানুষের চিন্তাকে না নাড়িয়ে যেতে পারে না। প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেবে আর সমাজে অনিয়ম অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রত্যেকেই এগিয়ে আসবে এ চাওয়া কেবল স্বপ্ন হতে পারে না।
মুরের সময়ে এ সম্ভাবনা ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক নিয়ম নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হলেও উনিশ শতকে এসে পুঁজিবাদী সম্ভাবনার নগর দ্বারে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে সমাজের সবচেয়ে নিম্ন বা দরিদ্র বা শ্রমিক শ্রেণির; এরই ধারাবাহিকতায় সর্বহারা শ্রেনীর উপরই সর্বদা বৃহৎ বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং একটি সমাজের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ব্যবস্থা টিকে থাকে এই শ্রেণিরই উপর যে শ্রেণি বরাবরই উপেক্ষিত। সবধরনের শ্রেণি লুপ্তের মাধ্যমে যে সমাজ গড়ে উঠে তাই কমিউনিস্ট সমাজ।
জাহেদ সরওয়ারের রচনা-সন্দর্ভে তাই ‘কমিউনিস্ট পার্টির ঘোষণাপত্র বা ইশতেহার’ও ঠাঁই পেয়েছে স্বাভাবিকভাবে। মার্কস ও এঙ্গেলস ‘ডেমোক্রেটিক এসোসিয়েশন’ গঠনে অংশগ্রহণ করেন যে সংগঠনের মাধ্যমে তারা ব্রাসেলসের গণতন্ত্রী এবং অন্যান্য দেশের প্রবাসী গণতন্ত্রীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। এই সংগঠনে তারা বলতেন যে সর্বপ্রকার প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক আন্দোলন সমর্থন করা হচ্ছে প্রলেতারিয়েতের দায়িত্ব। ১৮৪৭ সালে নভেম্বর মাসে প্রাথমিক নাম ‘ধর্মপত্র’ এর পরিবর্তে ‘কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার’ নাম রাখার প্রস্তাব করেন এঙ্গেলস।
এঙ্গেলস মার্কসকে চিঠিতে লেখেন, ‘…লেখা হয়েছে সহজ, সরল বর্ণনামূলক ভাষায়…। শুরুতে আমি ব্যাখ্যা করেছি কমিউনিজম জিনিস কি, তারপর সোজা চলে যাই প্রলেতারিয়েতের কথায়, তার উৎপত্তির ইতিহাস, পূর্বেকার কর্মীদের মধ্যে পার্থক্য, প্রলেতারিয়েত এবং বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধিতার বিকাশ, সংকট, উপসংহার…।’
প্রাবন্ধিক স্বল্প আয়তনে বইটি সম্পর্কে বিস্তারিত আর ঐতিহাসিক তথ্য সংবলিত বিবরণ না দিতে পারলেও ইশতেহারের উদ্ভব ও প্রয়োজনীয়তার সাথে উৎপাদনের সম্পর্ক ও উৎপাদন ব্যবস্থার কথা পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলেননি। উৎপাদন আর বিনিময় প্রথা-ই সমগ্র সম্পর্কের মূল হোতা। মোদ্দা কথা, কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার কেবল রাজনীতির দলিলই নয় আর তা কেবল একবার পড়লেই শেষ হয়ে যায় না; বরং উন্নত ব্যবস্থার পথে প্রলেতারিয়েত থেকে শুরু করে সব শ্রেনীর বিলুপ্তির প্রয়োজনে গভীর মনোনিবেশে বইটি বারবার পড়া উচিত।
প্রাবন্ধিক জাহেদের সুণিপণ কারিগরি কৃতিত্ব হচ্ছে প্রবন্ধের মশলা সংগ্রহে তিনি ঘুরে বেরিয়েছেন গোটা পৃথিবী এবং চষে বেরিয়েছেন বিভিন্ন সময়। ১১২ পৃষ্ঠার ‘পরদেশী বই’ টিতে মাই দাগেস্তান/কবির শ্রেণি চেতনা, ভয়েজেস ফ্রম চেরনোবিল/পরমাণু যুদ্ধের পরের পৃথিবী, মাই ডেইজ/ আর কে নারায়ণের আত্মজীবনী ইত্যাদি আরও চমৎকার নিবন্ধ রচনায় সুরুচির ছাপ রয়েছে স্পষ্ট।
প্রতিটি প্রবন্ধ ৪/৫ পৃষ্ঠার বেশি নয়। দীর্ঘ আলোচনা না হলেও ছোট ছোট সাঁতার কেটে লেখক মানব চিন্তার ধারাবাহিকতায় বেশ কয়টি চিন্তকের সমুদ্রে আমাদের উৎসাহ যুগিয়েছেন পাড়ি দেবার। শিল্প, সাহিত্য তত্ত্ব, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস-সবকিছুর গল্প করে গেছেন সাবলীল সাহিত্য পাঠের সুখ রোমন্থনে। পাঠক মাত্রই চুম্বকের মতো এই রোমন্থনে শামিল না হয়ে পারে না।
বই: পরদেশি বই
লেখক: জাহেদ সরওয়ার
প্রচ্ছদ:রাজীব দত্ত
প্রকাশক: দিব্য প্রকাশ
প্রকাশকাল: ২০১৯ ফেব্রুয়ারি
দাম: ২০০ টাকা
পৃষ্ঠা : ১১২