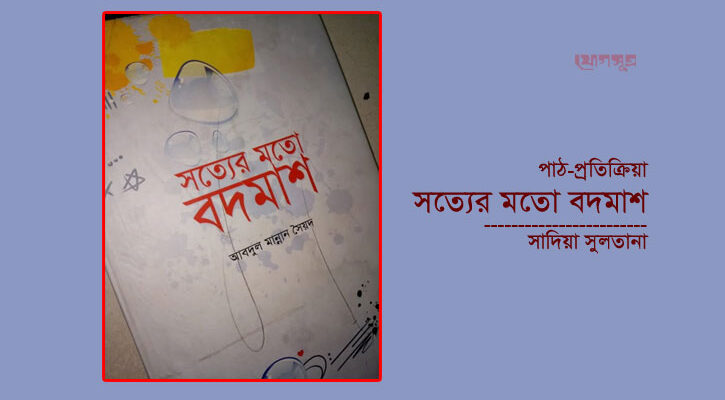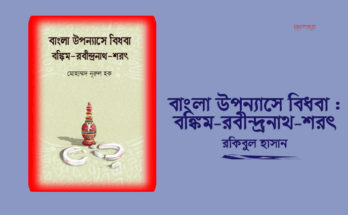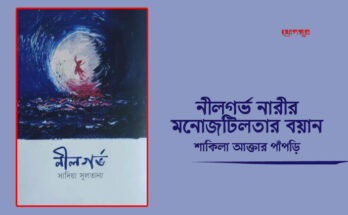বাংলাদেশের অন্যতম সব্যসাচী লেখক আবদুল মান্নান সৈয়দের গল্পের ভাষা, আঙ্গিক ও ইঙ্গিতধর্মী বিষয় বৈচিত্র্য তাকে তার সমসাময়িক ও বর্তমান সময়ের লেখকদের কোলাহলের মাঝেও স্বতন্ত্র স্থানে অধিষ্ঠিত করে রাখে। গল্প নির্মাণে আবদুল মান্নান সৈয়দের নিরীক্ষা প্রবণতা, শব্দ ও উপমার ব্যবহার এবং পরিমিতিবোধ পাঠককে যেমন আকৃষ্ট করে তেমনি সময়ে সময়ে পাঠককে বিপন্নও করে তোলে। পাঠক তাই গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের মতো মনোজগতের বিপুল রহস্যের ভেতরে খাবি খেতে খেতে তা থেকে উত্তরণের পথ খোঁজে।
‘দ্য প্যারিস রিভিউ’ এ প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকারে (নৈঃশব্দ্যের সংলাপ, বিশ্বসাহিত্যের নির্বাচিত সাক্ষাৎকার, ভাষান্তর ও সম্পাদনা এমদাদ রহমান) পর্তুগালের লেখক হোসে সারামাগো বলেছিলেন, ‘গল্পের যতগুলো চরিত্র থাকবে সবগুলোই গল্পের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। চরিত্রগুলো গল্পে এমন একটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে, গল্পের যে স্ট্রাকচারটি লেখক সৃষ্টি করতে চাইছেন, সেখানে লেখককে তারা সাহায্য করবে।’ ঠিক তেমনটাই দেখি আবদুল মান্নান সৈয়দের কালজয়ী গল্প ‘সত্যের মতো বদমাশ’ গল্পে। গল্পটি পড়তে পড়তে মনে হয় মা, ছেলে, কথা বলা লাল ঠোঁটের টিয়েপাখি, শাদা দাড়ির বুড়ো, কাগজের সাপ থেকে শুরু করে ছেলেকে কবরে যাবার খাটিয়ার চারটি পায়ার মতো বয়ে নিয়ে চলা নিরুত্তর চারজন লোক পর্যন্ত প্রত্যেকটি চরিত্রই গল্পের পূর্ণতার জন্য দরকার ছিল। গল্পের কোনো চরিত্রই হয়তো এককভাবে প্রধান হয়ে ওঠেনি তবে গল্পের নামকরণের ভেতরে যেই সত্য লুক্কায়িত আছে তার জন্য চরিত্রগুলোর উপস্থিতি অনিবার্য ছিল। যতবার ‘সত্যের মতো বদমাশ’ গল্পটি পড়ি ততবারই মনে হয় একটি বন্ধনীর ভেতরে আটকে থাকা শব্দ তিনটি মানবজীবনের অযুত-নিযুত গুঢ় সত্যকে ধারণ করে থাকে যা আবিষ্কার করার জন্য ধ্যানী হতে হয়। এই গল্পে এক কিশোর তার মায়ের সঙ্গে মেলায় যায়।
মায়ের মুখমণ্ডল থাকে তৈলাক্ত করুণ ও লম্বিত আর কিশোরের গোল মুখ তাকে বিস্ময় আনন্দ ও কৌতূহলে ভরা। মা, ছেলে দুজনই এক মুষ্টি অথচ সমুদ্রসমান এই গ্রহের মেলার মধ্যে এসে ঢোকে। ঘুরতে ঘুরতে আনন্দের পাশাপাশি ভয়ও এসে ভর করে ছেলের মনে, সে সামান্য ছায়া দেখেও ভয়ে কুঁকড়ে যায়। মা ছেলেকে স্বস্তি দিতে বলেন, ‘ছায়া সব সময় তোর সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরবে, হয় পেছনে না হয় সম্মুখে, ছায়া নেই এরকম কোনো মানুষ আমি দেখিনি। ভয় কী, অমন করে উঠলি কেন?’ কিশোর মায়ের কথায় সত্যি পায় না, সে মুহুর্মুহু মাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে। ধীরে ধীরে তার সরল চোখের সামনে প্রকট হয়ে উঠতে থাকে প্রাণীকূলের শয়তানি। বিপন্ন কিশোর তাই মাকে বলে, ‘আচ্ছা মা, তুমিই বলো আমার গা ছুঁয়ে, যে পাখি কথা বলতে শেখে, সে কি আর পাখি থাকে? সে তো একটা বদমাশ হয়ে যায়।’ একসময় সব ভয়, সব আশংকা সত্যি করে কিশোরের মা মেলায় হারিয়ে যায়। কিশোর বুঝতে পারে না, তার মা কি সত্যি হারিয়ে গেছে, না যারা তাকে জোরজবরদস্তি করে নাগরদোলায় তুলে নিতে চেয়েছিল তারাই মাকে ছিনতাই করে নিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত কিশোরের পরিণতিও ভয়াবহ কিছুর ইঙ্গিত দেয়।
মা-ছেলের মধ্যকার সম্পর্ক আর টানাপোড়েন নিয়ে আবদুল মান্নান সৈয়দের একটি উল্লেখযোগ্য গল্প ‘মাতৃহননের নান্দীপাঠ।’ ‘পৃথিবীতে মা আমাকে সবচেয়ে ভালোবাসেন, এবং আমি তাঁকে’-আপাতদৃষ্টিতে বাক্যটি সরল ও চিরন্তন সত্যের ইশারা করলেও কথাসাহিত্যিক আবদুল মান্নান সৈয়দের ‘মাতৃহননের নান্দীপাঠ’ গল্পের পাঠ পরিক্রমায় পাঠক জটিল থেকে জটিলতর এক পরিস্তিতির মুখোমুখি হয়। এই গল্পে মায়ের আচরণ যখন একজন সন্তানের মনে ঘৃণা আর আক্রোশের জন্ম দেয় তখন সন্তান মাকে হত্যা করার মতো সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়। ‘মাতৃহননের নান্দীপাঠ’ গল্পের কিছু শব্দ কিছু বাক্য এত বেশি তীক্ষ্ম যে পাঠকও মাকে হত্যার জন্য সন্তানের পক্ষে যুক্তি খুঁজে পায়। পাঠকেরও মনে হতে থাকে, ‘মায়ের দুটি নির্নিমেষ চোখ পিছনে ছুটছে, পিছলে পড়ছে না একবারো, সরে যাচ্ছে না, এমনকি পলক ফেলছে না কখনও, যেন মানুষের চোখ নয়। মানুষের অবশ্য, তবু মানবীয় নয়।’ মূলত মানবিক সম্পর্কের টানাপোড়েনই মা ও ছেলের মধ্যে এই বিভাজন সৃষ্টি করছে। যার শুরু এবং শেষ হন্যে হয়ে খুঁজতে হয়। বিষয় বৈচিত্র্যে আবদুল মান্নান সৈয়দের গল্প অনন্য, এই গল্পও তাই। এর ভাষা শৈল্পিক এবং পরিপ্রেক্ষিত আমাদের জীবন সম্পর্কিত হলেও খুব বেশি চেনা নয়। মূলত একজন যুবকের মনোজগতের দ্বন্দ্ব নিয়ে গল্পের টানটান আখ্যান গড়ে উঠেছে। একটা সময়ে যুবক নিজেই স্বীকার করছে, ‘আমি একজন অস্বাভাবিক প্রকৃতির মানুষ-নির্জনতা সর্বনাশ করেছে আমাকে।’
আবদুল মান্নান সৈয়দের আরেকটি আলোচিত গল্প ‘চাবি।’ এই গল্পে চিত্রকলার একজন তরুণ অধ্যাপক একদিন ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পকেটে হাত রেখে টের পান, তার ঘরে ঢোকার চাবিটি হারিয়ে গেছে। এরপর তিনি চাবির খোঁজে প্রতিবেশীদের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ান। কিন্তু দরজা খুলে তাদেরকে খুব একটা আন্তরিকতা নিয়ে অনাহূত অতিথি বা আগন্তুককে স্বাগত জানাতে দেখা যায় না। নাগরিক জীবনের বিচ্ছিন্নতা আমাদেরকে এমনই বিভেদের মুখোমুখি দাঁড় করায় যে পাশের ফ্লাটে বসবাস করা মানুষটিকেও আগন্তুক বলে বলে হয়। মূলত এই বিচ্ছিন্নতাবোধ শহরের মানুষের মনে বিরক্তি আর সন্দেহ প্রবণতা প্রবাহমান রাখে। এখানে অধ্যাপকেরও একই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়। আবার এমনও হয় যে কোনো একটা ঘরের দরজা খুলে যেতেই এক ঝাঁক নবীন ছেলেমেয়ে দেখা যায়, যাদের চঞ্চলতা আর কলহাস্য অধ্যাপকের মন ভালো করে দেয়। দরজা খুলে কেউ আবার ধমকের ভঙ্গিতে বলে, ‘বলছেন, আমাদের উপরের তেরো নম্বর ফ্ল্যাটে থাকেন আপনি? অসম্ভব, আপনাকে কোনোদিন এ অঞ্চলেই দেখিনি। আপনি মশাই চালাকি পেয়েছেন-আসুন, বাজি রাখুন দশ টাকা, বললাম: আপনি এ বাড়ির কোনো ঘরেই থাকেন না। এ বাড়ির লোকদের চেহারা অন্যরকম হয়, জানেন? চাবি খুঁজছেন, হ্যাঁ, চাবির কি হাত হয়েছে?’ এভাবে একটা চাবিকে কেন্দ্র করে শহরবন্দী মানুষের সম্পর্কহীনতা, অবিশ^াস আর পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা প্রকট হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত তেতলার সবচেয়ে কোনার ফ্ল্যাটের দরজা খুলে রহস্যময় নারীরা যখন জানায়, ‘চাবি পেলে আসবেন, এখানে কয়েকটি দরোজা-বন্ধ-করা ঘর আছে। আমরাও যে চাবি খুঁজছি গো’… তখন গল্পটি আর চাবির থাকে না। আর পাঠকও উপলব্ধি করে সে নিজেও ‘কয়েকটি দরোজা-বন্ধ-করা’ ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর খুঁজছে তার হারিয়ে যাওয়া চাবি যা হাতে পেলে সে তার কাক্সিক্ষত গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে।
‘অস্থির অশ্বখুর’ গল্পটিও একজন অধ্যাপককে কেন্দ্র করে আবর্তিত। তবে গল্পটি গল্পের চেয়ে বেশি কবিতার মতো মনে হয়। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র অধ্যাপক একজন কবি যার বুকের ভেতরে সারাক্ষণ ছেঁড়া উড়ো পঙক্তিমালারা ঘোরে। রাত্রিবেলা জেগে ওঠে কবির ঘর, যেখানে টেবিল ল্যাম্পের আলোর বলয়ে এসে বসতে না বসতেই মায়াবী জাদুবলে অক্ষরবন্দি হতে থাকে কবিতার পঙক্তি। কবির জীবনে ঘুরে ফিরে নারীরা আসে। মিনা, বিবি এমনকি বাড়ির কাজের মেয়েটিও তার সামনে দাঁড়ায় প্রাকৃতিক ভাস্কর্যের সৌন্দর্য নিয়ে। কখনও আগ্রাসী, কখনও বিষণ্ন সুন্দর দেখতে দেখতে কবি টুকরো টুকরো হয়ে পড়েন। তিনি উপলব্ধি করেন, সময় ছুটছে দুরন্ত এক ঘোড়ার মতো যার পায়ের নিচে তার জীবনের শত শত টুকরো শুধু স্পন্দিত হয়, কিন্তু গ্রথিত হয় না। শেষ পর্যন্ত কবি একটা সম্পূর্ণ কবিতাও লিখে উঠতে পারেন না।
‘গল্প ১৯৬৪’ গল্পে নিজের অতীতের গল্প বলছেন গল্পকথক কবির। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে বসন্তের উজ্জ্বল দুপুর, ঈষৎতপ্ত বাতাসে সদ্যস্ফুট আম্রমঞ্জরীর সুরভি, টিলার ওপরকার গাছের ছায়ারেখা, ভীরু চোখের খরগোশ এসে শ্রোতা আর কথককে আনমনা করছে। আর পাঠক ক্রমশ ঢুকে পড়ছে গল্পের ভেতরে। একটা সময়ে গল্পকথক কবিরের শহর যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে অশান্ত হয়ে ওঠে তখন তার সনাতন ধর্মাবলম্বী বন্ধু অমল তার বোন শোভাকে কবিরের হেফাজতে রেখে যায়। কবির ছিল দাঙ্গানিবারণী সমিতির সক্রিয় সদস্য। বোনকে অমল যেদিন ফিরিয়ে নিতে আসে তার আগের রাতে জৈবিক তাড়নায় একটা অপরাধ করে ফেলে কবির। কবিরের ভাষায় ‘সব-সমস্ত চলছিলো ঠিক। কিন্তু এক রাতে…আমার মধ্যে, জানোয়ার জেগে উঠেছিলো।’ ভেতরের পশুত্ব চাপা দিতে না পেরে অনুতাপ আর অনুশোচনায় দ্বগ্ধ হতে থাকা কবিরের বারবার মনে হচ্ছিল, অমল যদি আরেকটা দিন আগে আসতো তাহলে সে বেঁচে যেত। শোভা কিংবা কবিরের পরিণতি শেষ পর্যন্ত জানা না গেলেও মানুষের ভেতরের অবদমিত আকাঙ্ক্ষা তাকে কীভাবে তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারে তার একটা খণ্ডিত চিত্র দেখতে পাওয়া যায় ‘গল্প ১৯৬৪’ এ।
‘রাস্তা’ গল্পে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী সুস্থ, সবল দেহের অধিকারী এক যুবকের দিনলিপি হঠাৎ করে পাল্টে যায়, সে হারিয়ে ফেলে তার অতি চেনা অতি আপন বাড়ি ফেরার রাস্তা। সে পুরনো রাস্তার খোঁজে ছোটো, বড়ো, সোজা, বাঁকা অন্ধকার, আলোকিত কত রাস্তায় যে ছুটে বেড়ায় কিন্তু প্রতিবারই সে নিজেকে আবিষ্কার করে নতুন এক রাস্তায়। গল্পটি পড়তে পড়তে নতুন করে উপলব্ধি করি, জীবনের সমস্যা ‘যে পেরোতে পারে সে অবলীলাক্রমেই পেরোয়। যে পারে না, সে কেবল একই বিন্দুতে ঘুরপাক খায়।’ আসলে এই সত্যি হয়তো কারও কারও জন্য চিরন্তন, কারও কারও জন্য অপাংক্তেয় বা গুরুত্বহীন। ‘রাস্তা’ গল্পটিকে আপাতদৃষ্টিতে সাদামাটা মনে হলেও সমাপ্তিতে এসে গল্পটি ভিন্ন মাত্রা নিয়েছে। বলা যায়, রাস্তার রূপকে গল্পকার গণ্ডিবন্ধ মানুষের মধ্যে মুক্তি আর শৃঙ্খল ঘিরে তার যে মনোজাগতিক দ্বন্দ্ব তার একটা খণ্ডিত দৃশ্যপট উপস্থাপন করেছেন।
আবদুল মান্নান সৈয়দের গল্প পড়তে পড়তে আবিষ্কার করি তিনি গল্পের প্রধান, অপ্রধান চরিত্রের জন্য শুরুতেই একটি জাল তৈরি করতে শুরু করেন, ধীরে ধীরে চরিত্রগুলো ঐ জালে আটকে পড়তে থাকে আর বের হতে পারে না। গল্পকার সুকৌশলে পাঠককেও একই জালে বেঁধে ফেলেন। তাই স্বীকার করতেই হয়, আবদুল মান্নান সৈয়দের লেখার স্বকীয়তাই তাকে কাল, দশক নির্বিশেষে বাংলা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ করে রেখেছে।